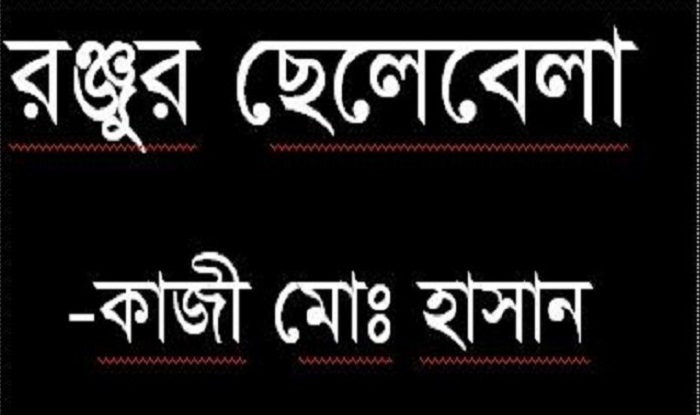-কাজী মােঃ হাসান
নতুন বাড়িতে এসেই ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি সামাজিক কাজে জড়িয়ে গেলেন আব্বু। প্রথম দিকে মসজিদ বানানো, ইয়ং ছেলেদের নিয়ে ক্লাব গঠন করা, পরে নিয়মিত ভাবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্ব দেয়াও প্রায় প্রতিদিনের রুটিনে পরিণত হলো । নির্বাচন আসতেই এলাকার লোকজন তাঁকে ধরে বসলেন- প্রার্থী হওয়ার জন্য।
প্রথম দিকে আব্বু পেশাগত কারণে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। এক সময় সবার চাপের রাজি হতেই হলো। নির্বাচনে দাঁড়ালেন তিনি।
তাঁর প্রতিদ্বন্দী একজন প্রাক্তন স্কুল মাষ্টার। খুব প্রতাপশালী। এক সময় স্থানীয় অত্যাচারি জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর কন্ঠস্বর ছিলো আগ্নেগিরিরর মতো সোচ্চার, প্রতিবাদ মুখর। তাঁর এ সাহসিকতা নিপিড়ীত জনগণকে খুব আন্দোলিত করে। চিন্তাা ও চেতনায় আনে এক বৈপ্লবিক জোয়ার। সবাই তাঁকে একজন সাহসি যুদ্ধা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে জনগণ তাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করে পরপর চার বার।
আর মুশকিলটা হয়েছে এখানেই। বার বার ভোটে পাশ করায় তিনি নিজকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেন। কাথা-বার্তায়, চাল-চলনে, এক কথায় কাজে-কর্মে ভাবখানা এমন যেন তিনি যা করেন, তিনি যা ভাবেন সেটা-ই ঠিক। এ তল্লাটে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এমন কেউ নেই। যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এমন কেউ আর আসবেও না। আসল কথা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে করতে একদিন তিনি নিজেই অত্যাচারি হয়ে উঠেন- যেন আর এক নব্য জমিদার।
নির্বাচনে আব্বুর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন তিনি। জুলুমের প্রতিবাদে জণগণ এক সময়ের প্রচ- জনপ্রিয় ব্যক্তিটিকে ছুড়ে দিলেন ডাষ্টবিনে।
জনগণ যা-ই করুক, নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য হলেও নির্বাচিত লোকটাকে মানতে পারলেন না তিনি। নির্বাচনের পর আব্বু তাঁর বাসায় গেলেন দেখা করতে। শুভেচ্ছা বিনিময় তো দূরের কথা, দেখা পর্যন্ত করলেন না। বরং সেদিন থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রুতা। সে এক ভিন্ন অধ্যায়।
কিছুদিন পরেই আব্বু একটা রেডিও কেনেন। তখন কিছু সংখ্যক শহরবাসি ছাড়া অনেকে জানতই না রেডিও জিনিসটা কি? শুধু ইউনিয়ন কেন, কয়েক থানায় খুঁজলেও রেডিও পাওয়া ছিলো খুব দুষ্কর।
কলেরগান বা মাইকের সঙ্গে সবাই কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু রেডিও আবার কি? এটার ব্যবহার দেখে সবাই খুব অবাক। আশেপাশের মানুষের একটাই জিজ্ঞাস্য- বাক্স কথা বলে কীভাবে? এছাড়া- এটা গান গায়, খবর বলে-এও কি বিশ্বাসযোগ্য? সবচেয়ে অবাক লাগে- কখন, কোথায় বৃষ্টি হবে, তুফান হবে,তাও বলে দেয় এটা। ‘বুনিয়াদী গনতন্ত্রের আসরে’ মজিদের মা, নসু ভাই, সাহেরা বুবু এরা কখন কোন জমিতে কোন ফসল বুনতে হবে, কোন সার ব্যবহার করতে হবে – তাও বলে দিতো এই বাক্সের ভেতর থেকে। এই নিয়ে গ্রাম্য মুরুব্বিদের মধ্যে ব্যাপক উৎকন্ঠা-
: হে আল্লাহ! ভাল মন্দ তুমিই জান! এই জাহেলিয়াতের যুগে আরও কত কী যে দেখমু!
তবে যে যাই বলুক, রঞ্জুর কাছে পল্লীগীতিটা ভীষণ ভালো লাগে। আব্বাসউদ্দিন, আবদুল আলীম, লায়লা আরমান্দ বানু, মাহবুবা রহমান, ফেরদৌসি, রওশন আরা, আঞ্জুমান আরা বেগম, আরো কত লোকের গান যে রেডিওতে বাজে তা বলে শেষ করা যাবে না! গান বাজলেই মানুষের ভীড় জমে।
নতুন বাড়িতে এসেই রঞ্জুদের জীবন ধারা একদম পাল্টে যায়। সবাই মনযোগ দেয় তাদের লেখাপড়ার দিকে।
রঞ্জুদের বাড়ি থেকে পোয়া মাইলের মধ্যেই বাবু সুরেন্দ্র কর্মকারের বাড়ি। শিক্ষিত লোক। বয়োবৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত দারোগা। অনেকটা সখের বশেই ইদানিং কয়েকটা বাড়িতে টিউশনি করে অবসর সময় কাটান। তাকেই রাখা হয় রঞ্জুদের প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে। ভীষণ বদ মেজাজী মানুষ! হবে না কেন? পুলিশের মেজাজ বলে কথা! একটু ভুলচুক হলেই সর্বনাশ- চর-থাপ্পর, কিল-ঘুষি তো আছেই, পিঠের উপর ধুমাধুম বেত চালাতেও কসুর করতেন না। আর এসব শাস্তি ছিলো নিত্য দিনের ঘটনা।
একদিন হলো কি! একটা সহজ বানান ভুল করায় স্যার রঞ্জুর উপর রেগে-মেগে আগুন। স্বভাবসুলভ ডান হাত বাগিয়ে ঘুষি মারলেন তিনি। এই ঘুষি লাগলে রঞ্জুর কী যে হতো, ভাবা যায় না! আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখে মাথা নামিয়ে নেয় রঞ্জু। ঢাল হিসেবে হাতের শ্লেটটাকেই তুলে ধরে সামনে। সাধারণতঃ শ্লেটের চারদিকে কাঠের বেড়ি থাকে। রঞ্জুর শ্লেটের সে বেড়িটা ভাঙ্গা। স্যারের ঘুষিটা সোজা এসে লাগে তার শ্লেটের কানায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতের তিনটা আঙ্গুল কেটে রক্তারক্তি। ব্যাপারটা দেখে স্যারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মিছির আলী কাকা। ডেটল, দুব্বা চিবিয়ে হাতে লাগিয়ে বন্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি।
কয়েকদিন পর্যন্ত হাতটা একদম অকেজো। গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হলেন স্যার।
আসলে, স্যারকে ব্যথা দেয়ার ইচ্ছে রঞ্জুর একদম ছিলো না। ঘুষি দেখে চোখের পলকে আপনা থেকেই শ্লেটটা চলে যায় সেদিকে। এই অপরাধের জন্য রঞ্জুকে সেদিন কান ধরে পঞ্চাশবার উঠ-বস করার সাজা ভোগ করতে হয়।
বৎসরের শুরুতেই আব্বু গোপাল ভট্টাচার্যের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিলেন রঞ্জুকে। স্কুলটা প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। বিরাট হল রুম। এখানেই সব ক্লাশ। শিক্ষক বলতে স্যার একা। শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁকে সহযোগিতো করে ক্লাশ ক্যাপটেন। দুষ্টুমি করে স্যারের চোখ এড়াতে পারলেও ক্যাপটেনের চোখ এড়ানো অসম্ভব। একটু কথা বললে, বা এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলের বন্ধুর কাছে ঢিল ছুড়ে মারলে আর রক্ষা নেই, তাকে টেবিলের উপড় দাঁড় করিয়েই ছাড়তো ক্যাপটেন। তারপর অপরাধ বুঝে স্যারের শাস্তি- চড়-থাপ্পর, নয় তো বেত। অন্যান্য শাস্তির মধ্যে ছিলো- হাটু গেড়ে বসিয়ে কপালে চারা রেখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করা, কান ধরে সমস্ত ক্লাশ প্রদক্ষিণ করানো, দু’পায়ের মাঝখানে মাথা দিয়ে উপুর করে রাখা। নয়তো, সবার সামনে ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়া। সুতরাং ক্লাশের সময় সবাই চুপচাপ।
একদিন, টিফিনের সময় রঞ্জুরা ক’জন বন্ধু মিলে জোগেশ বাবুর আমবাগানে গেলো ঘুরাফেরা করতে। তখন গাছে বোল থেকে সবে মাত্র ছোট্ট ছোট্ট কাচা আমের থোকা ঝুলতে শুরু করেছে। ঘুরাঘুরির ফাঁকে ঢিল মেরে আম পেরে খেতে গিয়ে কখন যে টিফিনের সময় পার হয়ে গেছে- বলতে পারেনি কেউ। ফিরে দেখে, অনেক আগেই ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে।
এখন উপায়? ক্লাশে ঢুকবে কি ভাবে? সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলেই স্যার ধরবেন। পেছন দিকে আছে ক্যাপটেন।
তারপরও পেছন দিকটাই নিরাপদ। সুযোগ বুঝে ক্লাশে ঢুকে পড়ে তারা। স্যার টের না পেলেও বাধ সাধে ক্যাপটেন। পথ আগলে দাঁড়ায় সে। আকারে-ইঙ্গিতে বহু অনুনয়-বিনয় কারার পরও ছাড়তে রাজি হলো না। বরং টেবিলের উপর দাঁড়াতে বাধ্য করলো সবাইকে।
রাগে কটকট করে তাকালেন স্যার। অপরাধ আগে ছিলো একটা, এখন দু’টো। এক- দেরি করে আসা, দুই- অনুমতি না নিয়ে চুপিচুপি ক্লাশে ঢুকতে চেষ্টা করা। বেতটা হাতে নিয়ে সাপের জিহ্বার মতো নাচাতে নাচাতে গম্ভীর ভঙ্গীতে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন স্যার।
প্রথমে চোখ লাল করে একে একে সবার কানটা ধরে কচলে (ঘষে) দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন- কোথায় কোথায় গিয়েছি। এ ক্ষেত্রে সত্য বললেও দোষ, আবার মিথ্যা বললেও দোষ। তাই সত্য কথাই বললাম সবাই। তিনি কি বুঝলেন কে জানে! দু’তিনটা বেত লাগিয়ে দরজার সামনে রৌদ্রে ‘নীলডাইন’ করে বসিয়ে দিলেন কপালে চাড়া বসিয়ে। নীলডাউনের চাইতে দশটা বেত খাওয়া অনেক ভালো। একে তো রৌদ্রের তাপ, তার উপর সূর্যের দিকে একটানা চেয়ে থাকা দারুণ কষ্টের । এ যেন হাশরের মাঠের ক্ষুদ্র নমুনা।
সময় যেন আর কাটে না। স্যারের মধ্যেও দয়ামায়ার চিহ্ন মাত্র নেই। তাই কষ্টটা চলে অবিরাম। শেষমেশ, আর কোনদিন এমন হবে না- এই শপথ নিয়ে শামিÍ থেকে মুক্তি দিলেন তিনি।
রঞ্জু বরাবরই ছাত্র হিসাবে খুুব ভালো না হলেও মোটামুটি ভালো। কিন্তু মানস অংকের মারপ্যাচ তার মাথায় কিছুতেই ঢুকতো না। অথচ সপ্তাহে দুই দিন এটা কম্পালসারি।
নিয়মটা এ রকম- মানস অংকের দিন স্যার ক্লাশের দু’জন ছাত্রকে কাছে ডাকতেন। একেবারে তাঁর টেবিলের সামনে। তারপর নির্দেশ দিতেন একে অন্যকে প্রশ্ন করার। প্রথম জন প্রশ্ন করে উত্তর দিতো দ্বিতীয় জন। আবার দ্বিতীয় জন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতো প্রথম জন। যে পারে তার তো পোয়াবার, না পারলে- ভাগ্যে বেত।
উত্তর না পারলেও রঞ্জু ক্লাশে যাওয়ার আগে খুব ভালো করে একটা মানস অংক মুখস্ত করে নিতো। স্যারের সামনে গিয়ে সেটাই ছুড়ে দিতো প্রতিপক্ষকে। আর ভাবতো, এবার কিছুতেই উত্তরটা দিতে পারবে না। কিন্তু তাকে হতবাক করে দিয়ে অপরপক্ষ এমন ভাবে উত্তরটা দিতো- যেন প্রশ্নটা ডাল-ভাত! অথচ উত্তর না দিতে পেরে প্রতিদিন-ই রঞ্জুর কপালে বেত খাওয়া ছিলো বান্ধা।
বলা যায়, মানস অংক নিয়ে দুশ্চিন্তায় দু’তিন মাস ধরে খুব কষ্টেই যাচ্ছিলো রঞ্জুর দিনকাল। বাড়ির স্যার কত ভাবে বুঝাতেন- বিষয়টা এভাবে নয়- এভাবে। প্রথমে মনযোগ দিয়ে প্রশ্নটা শুনবে। তারপর যোগ, বিয়োগ, গুণ-ভাগ- এসব অংকের মতোই সমাধানের কথা ভাবতে। দেখবে, সহজেই উত্তরটা এসে যাবে তোমার মাথায়।
কিন্তু স্যার যতই বুঝাক- রঞ্জুর অবস্থা তথৈবচ। কোন মতেই মানস অংকের মারপ্যাঁচটা মাথায় ঢুকতে চায় না। যেদিন মানস অংক থাকে, তার আগের রাতে রঞ্জুর ভালো করে ঘুমু পর্যন্ত হয় না। শরীরে জ্বর উঠে যেতো একশ’ চার ডিগ্রী। ঝর ঝর করে ঘেমে হাত-পা অবশ। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা! শত চাইলেও মানস অংকের ভীতিটা মাথা থেকে তাড়াতে পারে না।
সময়টা বৎসরের মাঝামাঝি। একদিন বাড়ির উঠানে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে ছয়গুটি খেলছিলো রঞ্জু। খুব দেখেশুনেই চাল দিচ্ছিলো দু’জনে। গুটির চাল দেবার এক পর্যায়ে হঠাৎ করেই মানস অংকের ঘোরপ্যাচটা ধরা পড়ে তার মাথায়। ঐশী কারবার যেন! আর যায় কোথায়! খুশীতে ডিং ডিং করে নাচতে নাচতে ঘরে গিয়ে মানস অংকের বইটা নিয়ে নিজে নিজেই পরীক্ষা করে দেখে কয়েকবার। সবকিছু ঠিক মতো পারছে কি-না?
হ্যাঁ হ্যাঁ সে পারছে। একদম ঠিক ঠিক পারছে। সে যা যা ভাবছে, উত্তরটা ঠিক তাই হচ্ছে। রঞ্জুর পক্ষে খুশিটা ধরে রাখা অসম্ভব। তাই, নাচতে লাগলো সারা ঘর জুড়ে। তার এই নাচ দেখে উঁকিঝুঁকি মেরে হাসতে থাকে বাড়ির সবাই। তবে কেউ বুঝতে পারছে না- আসল বিষয়টা কি! এদিকে স্কুলে চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত, রঞ্জুও এ নিয়ে কারো কাছে মুখ খুলতে নারাজ।
স্কুলেও সে সফল। বেঁচে যায় বেত খাওয়া থেকে। সেই শুরু। মানস অংকটা তার কাছে এখন পানিভাতের মতো সোজা। ক্লাশের প্রশ্নত্তোর পর্বে সে শুধু উত্তরই দেয় না, কঠিন থেকে কঠিন প্রশ্ন করে অপর বন্ধুকে থ বানিয়ে ছাড়ে। একেই বলে সাধনা।
বিজয়ের এই নেশাটার জন্যই বৎসর শেষে ক্লাশে প্রথম হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় সে।
(চলবে……………)
(“রঞ্জুর ছেলেবেলা” থেকে)